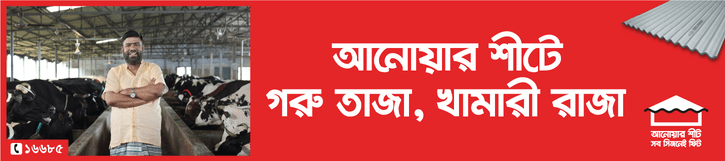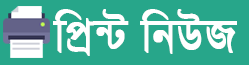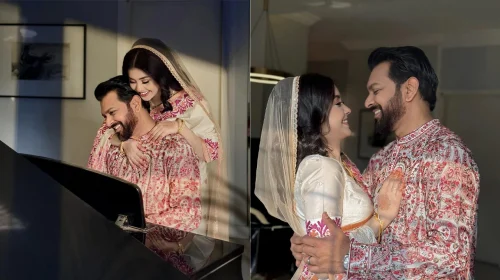প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘাত, বাস্তুচ্যুতি বা মানবিক বিপর্যয়ে সরাসরি প্রভাব পড়ে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অঞ্চলভেদে দুর্যোগ যখন আসে, তখন শুধু অবকাঠামো নয়; বিপর্যস্ত হয় মানুষের জীবনও। কিন্তু মানসিক রোগের চিকিৎসাব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সারা দেশে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে মানসিক সমস্যা এবং এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে এ ধরনের রোগী ৩ কোটি। এর মধ্যে চিকিৎসাসেবার বাইরে রয়েছে ৯০ শতাংশ। আর এক-তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যায় আক্রান্ত হন।
এমন পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের মতো আজ বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস-২০২৫। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য-‘অ্যাকসেস টু সার্ভিসেস-মেনটাল হেলথ ইন ক্যাটাস্ট্রোফেস অ্যান্ড ইমার্জেন্সিস’ অর্থাৎ বিপর্যয় কিংবা জরুরি অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা যেন পাওয়া যায়। এবারের প্রতিপদ্যে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো-মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্তদের জন্য অর্থপূর্ণ সহায়তা ও চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সমাজের প্রচলিত ভুল ধারণা, কলঙ্ক ও বৈষম্য দূর করা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বার্তা দিয়েছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব তার বার্তায় বলেন, ‘আমরা এক কঠিন পরীক্ষা ও সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। সংঘাত, স্থানচ্যুতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অসংখ্য মানুষ মানসিক চাপ ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। এই বছরের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী, জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। দিবসটির বার্তায় মহাসচিব জানান, সংঘাতে আক্রান্ত প্রতি পাঁচজনের একজন মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভোগেন, অথচ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও সহায়তা পাওয়া যায় না। মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি অপরিহার্য। জরুরি প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবেই মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
এদিকে বিশেষজ্ঞরা জানান, জাতিসংঘের মহাসচিব যে পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন, বাংলাদেশের চিত্রও প্রায় একইরকম। দেশে দৃশ্যমান দুর্যোগ কম হলেও এখানে প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন। দুর্যোগপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর মতো দেশেও মানসিক সচেতনতা ও স্বাস্থ্যের চিকিৎসা ঘাটতি আছে।
মানিসক স্বাস্থ্য নিয়ে বেসরকারি এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. মুনাইম রেজা মুনিম একটি গবেষণা করেছেন। ‘পাথওয়ে টু মেন্টাল হেলথ সার্ভিস’ অর্থাৎ মানসিক রোগীরা মানসিক স্বাস্থ্যসেবাদাতাদের কাছে পৌঁছাতে কোন কোন ধাপ অতিক্রম করেন। মানসিক সমস্যাজনিত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালটিতে আসা ৫০ জন রোগীর কাছে জানতে চাওয়া হয় কতদিন ধরে রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে এবং একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ দেখানোর আগে রোগীরা কোথায় কোথায় সেবা নিয়েছেন। গবেষণায় দেখা যায়, একজন রোগীর রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর থেকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবাদাতা চিকিৎসকের কাছে যেতে তার সময় লেগে যায় গড়ে ৩৮ মাস। কারও কারও ক্ষেত্রে ২০ বছর পর্যন্ত। এছাড়া সমস্যা দেখা দেওয়ার পর সঠিক মনোরোগ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের কাছে আসার আগে গড়ে একজন রোগী পাঁচবার ফার্মাসিস্ট, সাধারণ চিকিৎসক, হুজুর, কবিরাজ বা অন্যদের কাছে গেছেন। শতকরা ২৪ জন যান হুজুর ও কবিরাজের কাছে। ২১ জন যান বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক যেমন : হৃদরোগ, কিডিনরোগ অথবা গ্যাস্ট্রোএন্টিরোলজিস্টের কাছে। ফার্মেসিতে যান ১৭ ভাগ। মাত্র ১৫ শতাংশ যান মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে।
ডা. মো. মুনাইম রেজা মুনিম যুগান্তরকে বলেন, সঠিক চিকিৎসকের কাছে সময়মতো না যাওয়ায় বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হয়। এতে তাবিজ, পানি পড়া, ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করেন। যেটি তার প্রতিষেধক নয়। চিকিৎসকের কাছে না যাওয়ার কারণ হিসাবে অনেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদু, শারীরিক রোগ ছাড়া মানসিক রোগ নেই ইত্যাদি মনে করেন। রোগীরা গ্রামের ফার্মেসির ফার্মাসিস্টদের চিকিৎসক মনে করেন। এছাড়া সামাজিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে-এমন আশঙ্কায় চিকিৎসকদের কাছে আসতে চান না অনেকেই। এর জন্য সচেতনতা তৈরি, রোগের চিকিৎসা সবখানে পৌঁছানো দরকার।
এদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, মানসিক সমস্যা ও রোগের চিকিৎসার জন্য সারা দেশে সরকারিভাবে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট হাসপাতাল, পাবনা মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতাল, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় হাসপাতাল রয়েছে। এছাড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোয়ও রয়েছে এ চিকিৎসাসেবা। পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি ক্লিনিক। কিন্তু এগুলো খুবই ব্যয়বহুল। সরকারি পর্যায়ে রোগীর জন্য শয্যা রয়েছে মাত্র ১২৪০টি, যা রোগীর তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত।
দেশে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ২০১৮-১৯ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট একটি জরিপ চালায়। ওই জরিপ বলছে, দেশে লঘু থেকে গুরুতর মাত্রার মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা প্রাপ্তবয়স্ক ১৭ শতাংশ (নারী ১৯ শতাংশ, পুরুষ ১৫ শতাংশ)। ১৮ বছরের নিচের জনগোষ্ঠী ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে সব বয়সির মিলিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীর (মনোচিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ও অন্যান্য প্রশিক্ষিত মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবী) সংখ্যা এক হাজারের কম। সমস্যাগ্রস্ত ৯০ শতাংশের বেশি ব্যক্তি চিকিৎসার বাইরে থাকছেন।
১৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (আইআইইডি) প্রকাশিত এক গবেষণায় বাংলাদেশের ১৯৬০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, এই ৬৩ বছরে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। আর ক্ষতি বেড়েছে চারগুণ। এ প্রসঙ্গে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. তৈয়বুর রহমান রয়েল যুগান্তরকে বলেন, প্রতিটি দুর্যোগে মানুষ যেমন শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনই তার ওপর মানসিক চাপও সৃষ্টি হয়। এতে পরবর্তী সময়ে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি হতে পারে। বিষণ্নতাজনিত হতাশা একিউট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার ও পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারের মতো রোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের রোগকে আমলে নেওয়া হয় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা এ ধরনের মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত হন, তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে একপর্যায়ে তারা স্থায়ী মানসিক রোগীতে পরিণত হন। ব্যক্তির নিজের ও পরিবারের ওপর চাপ তৈরি হয়। দুর্যোগকবলিত এলাকাগুলোয় পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি কর্মসূচির অংশ হিসাবে সেখানে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী কাউন্সেলরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সেখানে পদায়ন করতে হবে। যারা এ ধরনের পরিস্থিতিতে আক্রান্তদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করবেন।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যক্তির ওপর বিভিন্নভাবে মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন : দুর্যোগের আকস্মিকতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কারণে মানুষ শক, ভয় ও বিভ্রান্তি অনুভব করেন। বাড়িঘর, কাজ বা প্রিয়জন হারানোর অনুভূতি মানুষকে অসহায় করে তোলে। দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হিসাবে দুর্যোগের ভয়াবহ স্মৃতি বারবার ফিরে আসা, ঘুমের ব্যাঘাত এবং অতিরিক্ত সতর্কতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি ও অনিশ্চয়তা থেকে দীর্ঘদিন বিষণ্নতা ও উদ্বেগ তৈরি হয়। মানসিক চাপ ও হতাশা কমাতে অনেকে অ্যালকোহল বা মাদকদ্রব্যের আশ্রয় নিতে পারে। পরিবার বা সমাজে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে। বাড়িঘর হারিয়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেওয়া মানুষকে মানসিক চাপে রাখে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা মানুষের মনে ভীতি তৈরি করে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাফিজা ফেরদৌসি যুগান্তরকে বলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট (মনোরোগ বিশেষজ্ঞ) হলেন একজন মেডিকেল ডাক্তার যিনি ওষুধ দিয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। অন্যদিকে সাইকোলজিস্ট (মনোবিজ্ঞানী) হলেন একজন থেরাপিস্ট, যিনি মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং প্রধানত টক থেরাপি (কথা বলে চিকিৎসা) ব্যবহার করে মানসিক ও আচরণগত সমস্যাগুলোর সমাধান করেন। মানসিক সমস্যায় কেউ সাইকোলজিস্ট আবার কেউ সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে যাচ্ছেন। কিন্তু মানুষ সচেতনতা বাড়লেও কোন সময় বা রোগে কার কাছে যেতে হবে, সেটি সবাই জানে না। তিনি বলেন, রোগ হলেই চিকিৎসকের কাছে যাবে তা নয়। কখন কার কাছে যাবে, সেটি নির্ভর করে অসুবিধাটা কোন মাত্রায় হচ্ছে। অনেক সময় রোগী শিশু হলে সেটি বুঝতে পারে না। যেমন পারিবারিক কারণে বিরোধ তৈরি হলে সাইকোলজিস্টের কাছে যাবেন। আবার ভয়াবহ মাত্রার মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। ওষুধ সেবন করে স্বাভাবিক জীবনে আসবে। এটা সামাজিকভাবে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশে সাইকোলজিস্ট (মনোবিজ্ঞানী) সংকট আছে। স্কুল-কলেজগুলোয় নিয়োগ দিয়ে সংকট দূর করতে হবে।
কর্মসূচি : দিবসটি উপলক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ সকাল ৬টায় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস (বিএপি) উদ্যোগে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ‘রান ফর মেন্টাল ওয়েলবিং ৫ কিমি. ম্যারাথন’ অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএমইউতে মনোরোগবিদ্যা বিভাগের উদ্যোগে সচেতনতামূলক র্যালি ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।